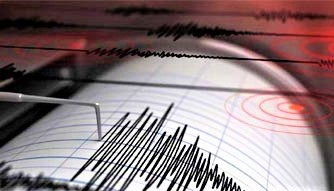*মু. জোবায়েদ মল্লিক বুলবুল*

মানুষ জন্মায় পরিবারে- বাস করে সমাজে আর মৃত্যুর পর শায়িত হয় মাটির বুকে। মানুষ জীবনের নানা ধাপ পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য, আর কবর হচ্ছে এই জাগতিক জীবনের শেষ ঠিকানা। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই শেষ আশ্রয়স্থলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সামাজিক, পারিবারিক, সমাধি ও মাজার সংস্কৃতির ধারণা। এ চারটি ধারণা শুধু দাফনের ব্যবস্থা নয় বরং তা জাতিগত, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক নানা দিক বহন করে। তবে শেষ শয়নস্থল কোথায় হবে- সামাজিক গোরস্থানে, না পারিবারিক কবরস্থানে, নাকি সমাধিতে, কিংবা মাজার বা সমাধিতে- তা নির্ভর করে ধর্মীয় বিধান, পারিবারিক ঐতিহ্য, আধ্যাতিকতা, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর। বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এই চার ধরনের শয়নস্থলের প্রচলন রয়েছে। কোথাও ধর্মীয় অনুশাসন, কোথাও সামাজিক চাহিদা, কোথাও জমি ও সম্পত্তির মালিকানা, আবার কোথাও ধর্মীয় বুজুর্গ বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কারণেই এ ভিন্নতা গড়ে উঠেছে।
ইসলামের ইতিহাসে গোরস্থান বা কবরস্থানের গুরুত্ব বহুপ্রাচীন। ইসলামে মৃত্যুর পর দাফন করা ফরজে কেফায়া। কবরস্থান পবিত্র, অটুট এবং সম্মানের স্থল হিসেবে বিবেচিত। হাদিসে রয়েছে- ‘তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সম্মানের সাথে দাফন করো’। মদিনার জান্নাতুল বাকি (জান্নাতুল বাকী) সামাজিক গোরস্থানের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ- যেখানে হাজারো সাহাবি, পরিবার, নবীজি (স.)-এর স্ত্রীগণ, সন্তানগণ সমাহিত। আবার অনেক সাহাবি ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ পারিবারিক স্থানে কবরস্থ করা হয়েছেন। যেমন মুআবিয়া (রা.) নিজ পরিবারের জায়গায় কবরস্থ হন। বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশে জমিদার বা প্রভাবশালী পরিবারগুলো বহু আগে থেকেই নিজেদের জমিতে পারিবারিক কবরস্থান গড়ে তুলেছেন। রাজশাহী, কুষ্টিয়া, বরিশালসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এমন পারিবারিক কবরস্থানের নিদর্শন দেখা যায়- যা আজও সংরক্ষিত রয়েছে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। নগরায়ণের চাপে কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে দ্রæত গতিতে, একইসঙ্গে সংকুচিত হচ্ছে গোরস্থান বা কবরস্থানের পরিসর। শহরাঞ্চলে মৃতদেহ দাফনের জন্য জায়গা খুঁজে পাওয়াই হওয় উঠেছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই বাস্তবতায় ‘গোরস্থান নিবন্ধন’ একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপেক্ষিত প্রশাসনিক বিষয়।
বাংলাদেশে গোরস্থান বা কবরস্থানের সঠিক সংখ্যা কত? তার কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই। তবে বাংলাদেশে কবরস্থানের সংখ্যা অনেক। দেশে হাজার হাজার সামাজিক গোরস্থান ও পারিবারিক কবরস্থান রয়েছে যেগুলোর অধিকাংশেরই সরকারি রেকর্ডে কোনো হদিস নেই। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে- বাংলাদেশে অনুমোদিত গোরস্থানের সংখ্যা প্রায় ৪৭ হাজার। সামাজিক গোরস্থান রয়েছে ৩৮ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ৮৫% গোরস্থান মসজিদ কমিটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। পারিবারিক কবরস্থান রয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার- যার বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকায়। গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৬৫% মানুষ সামাজিক গোরস্থানে দাফন হয়, ৩০% পারিবারিক কবরস্থানে এবং বাকিরা মিশ্র ব্যবস্থায়। ওই গবেষণায় বাস্তবতার প্রতিফলন নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। কোনো কোনো গোরস্থান বা কবরস্থান ৫০ বছর ধরে ব্যবহৃত হলেও সেগুলো এখনও অরেজিস্ট্রার্ড। ফলে জায়গার সীমানা নির্ধারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা কিংবা অবৈধ দখল রোধে প্রশাসন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না। একদিকে যেমন দাফন নিয়ে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন, অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন গোরস্থান বা কবরস্থানের কারণে নগর ব্যবস্থাপনা ও নগরায়নের সুষ্ঠু উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে।
বাংলা ভাষায় ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে চারটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ প্রায়শ ব্যবহৃত হয়- গোরস্থান, কবরস্থান, মাজার ও সমাধি। এসব শব্দের তাৎপর্য, ব্যবহার ও সামাজিক প্রতিফলন একে অপরের কাছাকাছি হলেও অর্থ ও প্রেক্ষিত ভেদে তাদের মাঝে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। শব্দগুলোর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্তি¡ক গুরুত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায়- গোরস্থান ও কবরস্থান সাধারণ দাফনস্থান। ‘গোরস্থান’ শব্দটি এসেছে আরবি ‘গোর’ বা কবর থেকে- যার অর্থ মৃতের দেহ সমাহিত করার জায়গা। ‘স্থান’ অর্থ জায়গা। অর্থাৎ গোরস্থান মানে হলো মৃতদেহ দাফনের জন্য নির্ধারিত স্থান। এই শব্দটি মূলত মুসলিম সমাজে প্রচলিত এবং বাংলার গ্রামীণ সমাজে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
‘কবরস্থান’ শব্দটিও প্রায় একই অর্থ বহন করে। যদিও কবরস্থান শব্দটি শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এটি আধুনিক বাংলা শব্দচয়নে বেশি প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে গোরস্থান ও কবরস্থান সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ জায়গাগুলোতে সাধারণত নামাজে জানাজার পর মৃতদের দাফন সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তীতে স্বজনেরা দোয়া ও কবর জিয়ারত করতে আসেন। অনেক এলাকায় সামাজিক গোরস্থান আলাদা করে নির্ধারিত থাকে এবং সেখানে বিশেষ ধরনের নিয়মনীতি পালন করা হয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক বা পারিবারিক দ্ব›েদ্বও গোরস্থানের জমি ব্যবহারের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে এটি কেবল ধর্মীয় প্রয়োজন নয়, সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীকও বটে।
সামাজিক গোরস্থান হচ্ছে এমন একটি জায়গা- যেখানে একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা সবাই মিলে সমবেতভাবে মৃতদের দাফন করেন। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় সরকার, সমাজ বা ওয়ক্ফ বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এখানে দাফনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও স্থান নির্ধারণ থাকে। শহরাঞ্চলে জমির সংকট ও জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে সামাজিক গোরস্থানের ওপর নির্ভরতা অনেক বেশি। সামাজিক গোরস্থানই দরিদ্র জনগণের জন্য একমাত্র দাফনের ব্যবস্থা। পারিবারিক জমি না থাকলে সামাজিক গোরস্থানই হয় শেষ আশ্রয়স্থল। সামাজিক গোরস্থান শুধু দাফনের স্থান নয় বরং এটি সামাজিক ঐক্য, শোক-সহানুভূতির কেন্দ্র।
জানাজা, দোয়া বা মোনাজাত ইত্যাদি সামাজিক রীতির অংশ। সামাজিক গোরস্থানে সবাই সমান। এখানে কোনো বড় পরিবার, শ্রেণি, বর্ণ নয়- শুধু মৃত্যুই সকলের পরিচয়। এটি ইসলামের ‘সমতা’ নীতির বাস্তব প্রতিফলন। ঢাকার আজিমপুর, বনানী, রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, মিরপুর কবরস্থান- all are public graveyards. বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বড় শহরগুলোতে কবরের জন্য জমি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
পরিকল্পনাহীন নগরায়ন এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। সরকারিভাবে অনেক জায়গায় সামাজিক গোরস্থান সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমÐলের তুরস্কে সামাজিক গোরস্থান বাধ্যতামূলক। পারিবারিক কবরস্থান শুধুমাত্র গ্রামের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। ইরানে সামাজিক গোরস্থান আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পারিবারিক প্রাইভেট প্লটও বরাদ্দযোগ্য।
পারিবারিক কবরস্থান মূলত একটি নির্দিষ্ট বংশ বা পরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত কবরস্থানের জায়গা। এটি সাধারণত পারিবারিক জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ পরিবার বা বংশের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের কবরস্থানে বাইরের কেউ সাধারণত দাফনের সুযোগ পান না। পারিবারিক কবরস্থানগুলো অনেক সময় ঐতিহাসিক দলিলের মতো কাজ করে। এখানে পুরুষানুক্রমিক কবর থাকে- যা একটি পরিবারের ইতিহাস বহন করে।
ইসলামে পারিবারিক কবরস্থানের বিষয়ে নিরুৎসাহনের কথা থাকলেও কোনো নিষেধ নেই। শর্ত হলো- কবর স্থায়ী, পরিচ্ছন্ন এবং সবার জন্য সমান মর্যাদার হতে হবে। পারিবারিক কবরস্থান পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান সংরক্ষণের প্রতীক। পারিবারিক কবরস্থানে পূর্বপুরুষের পাশে সমাহিত হওয়ার আকাঙ্খা ইসলামী আবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে বংশীয় মর্যাদা, দোয়ার ধারা অব্যাহত রাখা এবং পারিবারিক স্মৃতির সংরক্ষণে সুবিধা হয়। এটি স্বাধীন মালিকানায় রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হলেও, অনেক ক্ষেত্রে এটি বিতর্কের সৃষ্টি করে। শহরের জমি সংকটে পারিবারিক কবরস্থান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে ভূমি বিরোধ ও আদালতের মামলাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মাজার হচ্ছে আধ্যাত্মিক তীর্থস্থান। ‘মাজার’ শব্দটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে- যার অর্থ জিয়ারত বা পরিদর্শনের স্থান। এটি সাধারণ কবর থেকে আলাদা। মাজার শব্দটি সাধারণত ধর্মীয়ভাবে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যেমন ওলি, আউলিয়া, সুফি সাধক বা পীরের কবর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে অসংখ্য মাজার রয়েছে। যেমন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার সিলেটে, হযরত খাজা গরীব নেওয়াজের (রহ.) মাজার আজমিরে। এসব মাজার শুধু ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। মাজারে মানুষ মানত করে, দোয়া করে, কবর জিয়ারত করে এবং কখনো কখনো লোকগান বা আধ্যাত্মিক সংগীত আয়োজন করে। অনেক মাজারে আবার ওরস বা বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়- যা উৎসবে রূপ নেয়। তবে মাজার নিয়ে ইসলামী সমাজে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে একে তাওহিদের পরিপন্থী মনে করেন, আবার অনেকেই এটিকে ইসলামী আধ্যাত্মিক চর্চার অংশ হিসেবে দেখেন।
মৃত্যুর পর শেষ শয়নস্থলের অপর ধাপ সমাধি আধ্যাত্মিক স্তব্ধতার প্রতীক। ‘সমাধি’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘সম্’ (পূর্ণরূপে) ও ‘আধা’ (ধারণ) থেকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মে প্রয়াত গুরু, সাধক, মহাপুরুষ বা যোগীদের মৃত্যুর পর তাদের সমাধি তৈরি করা হয়। তবে এটি সাধারণ কবরের মতো নয় বরং এটি আধ্যাত্মিক তাত্তি¡ক স্তরকে প্রতিফলিত করে। সমাধি শুধু মৃত্যু নয়, চেতনাগত মুক্তির প্রতীক। অনেক হিন্দু সাধক জীবিত অবস্থাতেই সমাধিস্থ হন অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে দেহত্যাগ করেন। ভারতের পুনে শহরে লোকমান্য তিলক অথবা কাশীতে লাহিড়ি মহাশয়ের সমাধি- এসব ধর্মীয় ও দর্শনীয় স্থান হিসেবেও বিবেচিত হয়। শিখ ধর্মেও গুরুদের সমাধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাবে গুরু নানক দেবের সমাধি একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় সমাধির পাশে আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
গোরস্থান ও কবরস্থান হলো ধর্মীয়ভাবে সাধারণ মানুষদের দাফনের স্থান, মাজার হলো পূজ্যব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আর সমাধি হলো আধ্যাত্মিক স্তর অতিক্রম করা সাধুদের স্মৃতিসৌধ। শব্দগুলো কেবল মৃত্যুর চিহ্নমাত্র নয় বরং সমাজের ধর্মীয় আবেগ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এদের প্রতিটির পেছনে রয়েছে আলাদা ইতিহাস, ধর্মতাত্তি¡ক ব্যাখ্যা ও সামাজিক মর্মবোধ। এই পার্থক্যগুলো জানা সমাজকে ধর্মীয় সহনশীলতা ও ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট আইন নেই যা পারিবারিক কবরস্থান নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা দেয়। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার আইনে সামাজিক গোরস্থান ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল। অনেক সময় কবরস্থান দখল হয়ে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে- যা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে চরম অবমাননাকর। কবরস্থান আইনে সংযোজনী এনে পারিবারিক কবরস্থান নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং সামাজিক গোরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৩ একর জমি কবরস্থানের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।
সামাজিক গোরস্থানের ডিজিটাল নথি নিবন্ধনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে কার কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে তার রেকর্ড রাখলে পরিবারের পক্ষে পরবর্তীতে কবর খোঁজা সহজ হবে। পারিবারিক কবরস্থান নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করলে জমির দখল ও উত্তরাধিকার নিয়ে আইনি জটিলতা এড়ানো যাবে। নগর পরিকল্পনায় গোরস্থান অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গোরস্থান বা কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় ওয়াক্ফ বোর্ডের ভূমিকা জোরদার করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া কবরস্থানে দাফনের জন্য সমতার নীতিকে প্রধান্য দেওয়া উচিত। যদি প্রতিটি গোরস্থান বা কবরস্থান নিবন্ধিত হয়- তাহলে সেগুলোর জমির পরিমাণ, অবস্থান, ব্যবহারের ধরন ও মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে কেবল জমি রক্ষা নয় বরং পরিকল্পিত দাফন নীতিমালাও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় গোরস্থান কেবল দাফনের স্থান নয়, এটি একটি পবিত্র, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আবেগের স্থান। আজ যেসব গোরস্থান অনিরাপদ, অবহেলিত ও অব্যবস্থাপনার শিকার, সেখানে মৃতদের সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। একটি নিবন্ধিত, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল গোরস্থান বা কবরস্থান সেই সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।
এজন্য সরকারি পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে প্রতিটি গোরস্থান চিহ্নিত করে দ্রæত ডিজিটাল নিবন্ধনের আওতায় আনা জরুরি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে এসে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে গোরস্থান কমিটিকে নিবন্ধনের উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতে হবে।
গোরস্থান বা কবরস্থান কেবল মৃতদেহ দাফনের স্থান নয়, এটি একটি জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিচ্ছবি। সামাজিক গোরস্থান একদিকে ধর্মীয় সমতার শিক্ষা দেয়, অন্যদিকে পারিবারিক কবরস্থান সামাজিক মর্যাদা ও ঐতিহ্যের ধারক। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় সুসংগঠিত ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। গোরস্থানের নিবন্ধন মানে হলো আমাদের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের মধ্যকার এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন। তাই সময় এসেছে গোরস্থানের নিবন্ধনকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করার। তবেই মৃতদের প্রতি সম্মান, জীবিতদের প্রতি দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য একত্রে রক্ষা করা সম্ভব হবে।
লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক।