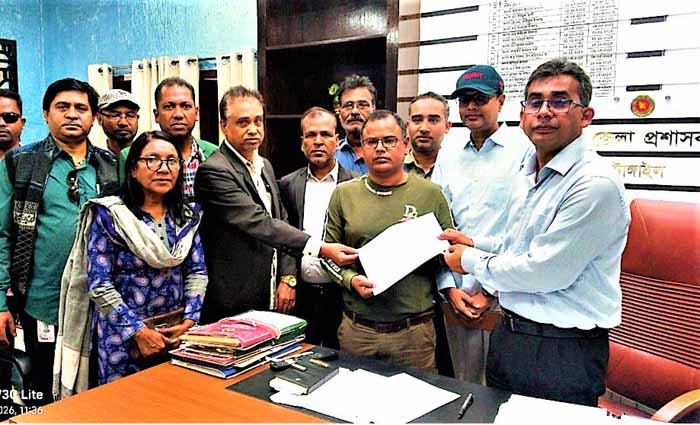*মু. জোবায়েদ মল্লিক বুলবুল*

বাংলার ইতিহাস কেবল রাজ্যপাট, রাজনীতি, জয়-পরাজয় ও যুদ্ধের ইতিহাস নয়; বরং বাংলার প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য, মাটি, কৃষি এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ইতিহাসই বাঙালির অস্তিত্বের বৃহত্তর পরিচয়। সেই পরিচয়ের একটি সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে মাটির কাছাকাছি উৎসব হলো নবান্ন। নতুন ধানের অন্ন যে শুধু খাদ্যের সূচনা নয়- এটি ছিল একটি মানসিক নিরাপত্তা, সমষ্টিক আনন্দ, উদারতার সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান, শ্রমের সম্মান এবং সামাজিক সংহতি।
আজকের দ্রæত পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে এই নবান্ন উৎসব- যা একসময় ছিল গ্রামবাংলার সবচেয়ে প্রাণের উৎসব, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন ধানের ঘ্রাণ টিনশেডের ঘর, দোচালা উঠোন, শালবন, খেজুরঝাড়, পুকুরপাড়, নারকেলবাগান, ধানক্ষেতের আল হয়ে এখন গুটিয়ে যাচ্ছে রেস্টুরেন্ট কেন্দ্রিক ‘নবান্ন উৎসব ফুড ফেস্ট’-এ। এ যেন সংস্কৃতির বাস্তব উৎসব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি সাজানো-দোকানদারি সিম্বলিক অনুষ্ঠানে পরিণত হওয়া।
বাংলার কৃষিকাজে সবসময়ই প্রকৃতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবান্নের উৎপত্তিও কৃষিনির্ভর বাঙালি জীবনের প্রাচীন এক অধ্যায় নির্ভর। ঋতুচক্রের সঙ্গে কৃষিকাজের যেসব পর্যায় যুক্ত- বোনা, চারা, রোপণ, পরিচর্যা, আগাছা পরিষ্কার, সেচ, বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ, পোকামাকড়ের হানা- এসবের মধ্য দিয়ে কৃষকের বছরজুড়ে স্থায়ী দুশ্চিন্তা ছিল স্বাভাবিক। তাই বছরের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ছিল ধান ওঠা। এবং সেই ধান ওঠার আনন্দের পরিণতই ‘নবান্ন’ অর্থাৎ ‘নতুন অন্ন’-এর উৎসব।
নতুন ধানের অন্ন পৃথিবীর বহু কৃষি সভ্যতাতেই একটি আনন্দের প্রতীক। যেমন- চীনে ‘হান শিং উৎসব’, জাপানে ‘নি-নাম-সাই’ দক্ষিণ ভারতের ‘পঙ্গল’, আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে ‘ইয়াম ফেস্টিভ্যাল’ ইত্যাদি। বাঙালির নবান্নও একই মানবিক অনুভূতির অংশ- খাদ্যের নিশ্চিততা, দুঃখ-কষ্টের অবসান, নতুন বছরের স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা। বাংলায় নবান্নের উৎপত্তি অন্তত দেড় থেকে দুই হাজার বছর পুরোনো বলে নৃতত্ত¡ববিদরা মনে করেন। বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি গড়ে ওঠার পর থেকেই নতুন অন্নকে কেন্দ্র করে একটি সামষ্টিক আনন্দধারা সৃষ্টি হয়েছে।
ধর্ম-সংস্কৃতি-লোকজ ঐতিহ্যের এক মহামিলন ‘নবান্ন’। নবান্নের সবচেয়ে অনন্য দিক- এটি কোনো একক ধর্মের নয়; এটি লোকধর্ম, লোকসংস্কৃতি। মুসলিম সমাজে নবান্ন পালিত হয় নানাভাবে। নতুন ধান আনার সময় মোনাজাত করা হয়। পায়েস, খিচুড়ির তৈরির আগে ফাতিহা পড়া হয়। মৃত পূর্বপুরুষদের রুহের মাগফিরাতের দোয়া পড়া হয়। গরিব-দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় ইত্যাদি কর্মসম্পাদন করা হয় খুবই ভক্তি ভরে। একইভাবে হিন্দু সমাজে নবান্ন পালনে ধর্মীয় আচার যোগ করা হয়। নতুন ধান দিয়ে ল²ী পূজা, ধানদেবীর উদ্দেশে নিবেদন, বাড়ি বাড়ি আলপনা আঁকা, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি, নতুন চালের পায়েস, খিচুড়ি, পিঠা ইত্যাদি তৈরি করা ও বিতরণ। নবান্ন উৎসব পালনে দুই সম্প্রদায়ের রীতিতে আচারগত পার্থক্য ছিল, কিন্তু আনন্দের একাত্মতা ছিল এক ও অভিন্ন। নবান্ন ছিল বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীকগুলোর একটি।
নবান্নের মৌসুমকে কেন্দ্র করে এক সময় কৃষিপঞ্জিকা ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও বিবেচিত হতো। যেমন- ঐতিহ্যগতভাবে নবান্ন পালিত হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, বিশেষ করে ১ অগ্রহায়ণ, আমন ধান কাটার পর। কিছু এলাকায় মাঘ-ফাল্গুনে বোরো ধান ওঠার পর ছোট আকারে ‘নবধান ভাত’ করা হতো। আঞ্চলিক ভিন্নতার কারণে নবান্নের সময়কালও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যেমন- তাপমাত্রা, নদীর পানি, বন্যা পরিস্থিতি, জমির ধরণ ইত্যাকার কারণে নবান্নের সময়কালে ভিন্নতা এসেছে।
নবান্নের আনন্দাচার তথা উৎসব গ্রামীণ সমাজকে একাকার করত। সেখানে কোনো জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ বিবেচিত হতো না। কারণ- নবান্নের শুরু হয় ধানক্ষেত থেকে। প্রথম ধান কাটেন- পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, কোথাও কোথাও বয়োজ্যেষ্ঠ নারী, কখনো প্রধান কৃষিশ্রমিক। প্রথম ধান কাটার সময়- ঢাক-ঢোল, বাঁশি, উলুধ্বনি, গান গেয়ে ধানের প্রথম আঁটি গুচ্ছ করা হতো। কেউ কেউ এটি ঘরের ধানের গোলার মাথায় বা ঘরের সামনে বেঁধে রাখতেন শুভ লক্ষণের প্রতীক হিসেবে।
নবান্নে রান্নাঘরজুড়ে নতুন চালের ঘ্রাণ ম’ ম’ করত। নতুন অন্ন দিয়ে রান্না করা হতো- পায়েস, নবান্ন খিচুড়ি, ঘি-ভাত, শুটকি-মরিচ-তেল দেওয়া ‘নবধান ভাত’, মুরগি বা হাঁসের ঝোল দিয়ে নবভাত, চিতই, পাটিসাপটা, ভাপা, চন্দ্রপুলি সহ নানা নামীয় পিঠা। গ্রামীণ নারীদের ‘শিল্পকলা’ পিঠা বানানোর মধ্য দিয়ে যেন ফুটে উঠত। সে সময়ের সমষ্টিক ভোজ ছিল সামাজিক সংহতির অমীয় বন্ধন। গ্রামের সবাই একসঙ্গে খেত। কোনো বাড়িতে আমন্ত্রণ কারও জন্যই ছিল না বাধ্যতামূলক- কারণ এটি ছিল উৎসবের মানবিক বন্ধন। নবান্নে বিনোদন ছিল অবশ্যম্ভাবী উপসঙ্গ। যেমন- লাঠিখেলা, পালাগান, বাউলগান, ধাঁধা প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা, ঘোড়দৌড়, কোনো কোনো এলাকার নদীপাড়ে নৌকা বাইচ ইত্যাদি। এসব সাংস্কৃতিক উপাদান নবান্নকে কেবল খাদ্য উৎসব নয়- এক বিশাল আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত করত। নবান্ন ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক। ধনু-সংক্রান্তি বা অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান উঠলে কৃষকের মনে বড় স্বস্তি আসত- ‘বছরটা কাটবে’ ভাবা হতো। নবান্ন কৃষকের ঘাম ও পরিশ্রমের সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হতো। নবান্নের ভোজ ছিল একধরনের সামাজিক থেরাপি- মানুষে-মানুষে দূরত্ব কমাতো। নবান্নে হিন্দু-মুসলিম মিলে একই উৎসবে অংশ নিয়ে অসাম্প্রদায়িক আদর্শের উদাহরণ রেখেছে- যা বাংলার নিজস্ব পরিচয়।
বাংলাদেশের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নবান্নের অনুপস্থিতি এক গভীর রোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে নবান্ন হারিয়ে যাওয়া কেবল একটি উৎসব হারানো নয়- এটি সামাজিক রূপান্তরের বড় সংকেত। কৃষি এখন পারিবারিক চৌহদ্দী পেড়িয়ে বাণিজ্যিক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। কৃষি যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নে এখন কৃষির রোপন ও কাটায় শ্রমিকের স্থান করে নিয়েছে ট্রাক্টর, ধানকাটার কম্বাইন হারভেস্টার, থ্রেসার, ধান মাড়াই, ভূট্টা মাড়াই মেশিন ইত্যাদি। এসবের প্রভাবে আগের মতো সম্মিলিত ধান কাটার আনন্দ নেই। নবান্নের অনুপস্থিতির জন্য নগরায়নও দায়ী। গ্রামে মানুষ নেই- গ্রামের যোগ্য ছেলে-মেয়েরা চাকরির জন্য শহরে আর বাবা-মা শহরের ফ্ল্যাটে অবস্থান করছে। সঙ্গত কারণেই পুরোনো বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। এতে নবান্ন করার পরিবেশই নেই।
বর্তমানে খাদ্যাভাব নেই, একই সঙ্গে নতুন ধানের বিশেষত্ব কমেছে। চাল-ডাল বাজারে সারা বছর পাওয়া যায়। খাদ্যপরিকল্পনা আগের মতো মৌসুমি নয়। ফলে সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়ছে। এখন- পারিবারিক ভোজ কম, প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্ক দূর বেড়েছে, উঠোন সংস্কৃতি নেই। তাই নবান্নও গ্রাম ছেড়েছে। এখন গ্রামের নবান্ন জায়গা করে নিয়েছে শহরের ব্যবসা কেন্দ্রে। কিন্তু ব্যবসায়িক ‘নবান্ন ফেস্টিভ্যাল’ সত্যিকারের নবান্ন নয়। শহরগুলোতে যা হয়- সেগুলোতে কৃষকের গন্ধ নেই। এটি ঐতিহ্য নয়, ব্যবসায়িক আয়োজন। প্রযুক্তি-নির্ভর এসব আধুনিকতা লোকসংস্কৃতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা জানে- হ্যালোইন, ক্রিসমাস, বø্যাক ফ্রাইডে। নবান্ন বা পিঠা-পুলি চেনা এ প্রজন্মের শিশুদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।
অথচ বাংলার সাহিত্য, গান, চিত্রকলা ও লোককথায় নবান্ন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নবান্ন বাংলা সংস্কৃতির প্রতিটি শিল্পমাধ্যমে অমলিন- জীবনানন্দ দাসের ‘ধানক্ষেতের গন্ধ’, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালীতে’ নতুন চালের পায়েস, জসীম উদ্দীনের ‘গ্রামবাংলা’, পল্লীগীতিতে নতুন ধানের গান, মহাকবি আলাওলের সময়েও নতুন অন্নের উল্লেখ, বাউল সুরে নতুন ফসলের সুখ ইত্যাদিতে। চিত্রশিল্পীদের তুলিতে- ধানক্ষেত, গোলাধান, খেজুরপাতা, নারীর পিঠা বানানো- এ সবই নবান্নের রূপ।
নবান্নের বিলুপ্তির গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্তি¡ক কারণও বিদ্যমান। যেমন- পারিবারিক ভাঙনের প্রভাব। যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে- নবান্ন একা করা যায় না। ভোগবাদী সংস্কৃতি উৎসবকে মূল্যহীন করেছে, শপিংমল-নির্ভর উৎসবে ঐতিহ্য নেই। কৃষকের প্রতি অবহেলা, কৃষকের অবমূল্যায়ন মানেই নবান্নের অবমূল্যায়ন। নবান্নের পুনরুজ্জীবনে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া অত্যাবশ্যক। যেমন- উপজেলা পর্যায়ে নবান্ন উৎসব আয়োজন, স্কুলে ‘লোকসংস্কৃতি সপ্তাহ’, কৃষক সম্মাননা ইত্যাদি উদ্যোগ যথাযথভাবে পালনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো পিঠা-পুলি মেলা, ধান-কাটা উৎসব ইত্যাদি সাংগঠনিক কর্মসূচি নিতে পারে। নবান্ন ফিরিয়ে আনতে মিডিয়াও ব্যাপক ও টেকসই ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন- টিভিতে নবান্ন ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার, রেডিওতে লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রচার, সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ইত্যাদি। গ্রামীণ নবান্ন ট্যুর, গ্রামভ্রমণ, পিঠা বানানোর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- নবান্নের পরিবার ভিত্তিক পুনরুজ্জীবন। পরিবারে শিশুদের নবান্নে যুক্ত করা গেলে নবান্নের পুনরুজ্জীবন ঘটবে- এটাই ভবিষ্যতের ভিত্তি।
হাল সময়ের এতো এতো পার্বনের ভিরে নবান্নকে কেন ফিরে পেতেই হবে?- এমন প্রশ্ন আসতেই পারে। কারণ- নবান্ন বাঙালির কৃষি-অর্থনীতির স্মৃতি, এটি পরিবার-সমাজের সেতুবন্ধন, এটি অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য, এটি খাদ্যসংস্কৃতির ভিত্তি, এটি মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক, নবান্ন প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা। নবান্ন হারালে আমরা শুধু একটি উৎসব হারাবো না- হারাবো আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি বিশাল অংশ।
নবান্ন ফিরে আসুক, বাংলাদেশ ফিরে পাক নিজের শেকড়। নবান্ন কেবল নতুন অন্নের উৎসব নয়- এটি আমাদের মাটির প্রতি দায়বদ্ধতা, আমাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, আমাদের সমাজের শক্তি, আমাদের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য এবং আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতি। এই স্মৃতি যাতে মুছে না যায়, এই উৎসব যাতে ব্যবসায়িক আয়োজনে বিলীন না হয়, এই ঐতিহ্য যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অচেনা না হয়। সেজন্য এখনই প্রয়োজন- গবেষণা, সংস্কৃতি রক্ষা, পরিবারভিত্তিক চর্চা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। নবান্ন ফিরে এলে বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ, বাংলার সমাজ- সবই আরও জীবন্ত হয়ে উঠবে। নবান্ন আজ হারিয়ে যেতে বসেছে- এ সত্য যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি শিক্ষণীয়। কারণ কোনো জাতি নিজের শেকড় ভুললে দাঁড়ানোর জায়গাটা দুর্বল হয়ে যায়। নবান্ন পুনরুজ্জীবিত করা মানে শুধু একটি উৎসব ফিরিয়ে আনা নয়; প্রাণের উৎসব নবান্ন আবার গ্রামে-গঞ্জে ফিরে আসুক- এটাই প্রত্যাশা।
লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক।